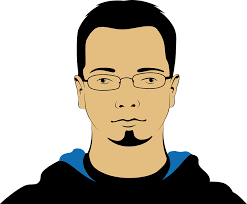

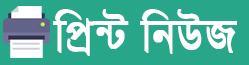
পাণ্ডুলিপি
আখতার হোসাইন খান
বিশ্বায়নের যুগে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সেবাপ্রদানে এসেছে মৌলিক পরিবর্তন। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। এই প্রেক্ষাপটে ই-গভর্ন্যান্স বা ইলেকট্রনিক প্রশাসন একটি কার্যকর ও সমসাময়িক ধারণা, যা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রশাসনকে আরও গণমুখী, গতিশীল এবং কার্যকর করতে সাহায্য করে। বাংলাদেশসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে ই-গভর্ন্যান্স ধীরে ধীরে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই প্রবন্ধে গণতান্ত্রিক প্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্সের ভূমিকা, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
ই-গভর্ন্যান্স বলতে বোঝায় সরকার ও জনগণের মধ্যে প্রযুক্তিনির্ভর যোগাযোগ ও সেবাপ্রদান ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নাগরিকরা দ্রুত ও সহজে সরকারি তথ্য ও পরিষেবা গ্রহণ করতে পারেন। এর মূল উপাদানগুলো হলো- G2C (Government to Citizen) – জনগণের কাছে সেবা পৌঁছানো (যেমন: জন্মনিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, শিক্ষা সনদ) , G2B (Government to Business) – ব্যবসার সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন (যেমন: ট্যাক্স পরিশোধ, ব্যবসায়িক অনুমোদন), G2G (Government to Government) – আন্তঃপ্রশাসনিক সমন্বয় ও তথ্য আদান-প্রদান, G2E (Government to Employee) – সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন (যেমন: পে-রোল ম্যানেজমেন্ট)
গণতান্ত্রিক প্রশাসনে ই-গভর্ন্যান্সের ভূমিকা – স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি-ই-গভর্ন্যান্সের মাধ্যমে তথ্যের উন্মুক্ততা নিশ্চিত হওয়ায় প্রশাসনে স্বচ্ছতা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকল্প ব্যয়, অগ্রগতি ও ফলাফল প্রকাশের ফলে দুর্নীতি কমে এবং জনগণ প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখে। নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা-অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ দিতে পারে, যা নীতিনির্ধারণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এটি গণতন্ত্রের একটি মূল উপাদান—‘people’s participation in governance’-কে বাস্তবে রূপ দেয়। সেবা প্রাপ্তির সহজতা ও গতিশীলতা- ই-গভর্ন্যান্সের ফলে জনগণকে আর অফিসে লাইন দিয়ে ঘুরতে হয় না। ভূমি সংক্রান্ত দলিল, পাসপোর্ট আবেদন, ট্রেড লাইসেন্স, জন্মনিবন্ধন—সবকিছুই অনলাইনে করা সম্ভব হচ্ছে, সময় ও খরচ দুই-ই বাঁচছে। দুর্নীতি হ্রাস- মানুষ-নির্ভর সিদ্ধান্তের বদলে স্বয়ংক্রিয় ও তথ্যনির্ভর কার্যপ্রণালী দুর্নীতির সুযোগ কমিয়ে দেয়। যেমন, ই-প্রকিউরমেন্ট বা ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম দ্রুত, সুশৃঙ্খল ও ভুল-কম হয়। কাগজপত্রে কাজের বদলে ডিজিটাল ডেটা সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুবিধায় সিদ্ধান্ত গ্রহণেও গতি আসে।
বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্সের বর্তমান বাস্তবতা – বাংলাদেশ সরকার “ডিজিটাল বাংলাদেশ” ধারণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদাহরণ হলো:একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প,উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার (UDC) – গ্রামীণ জনগণের কাছে ই-সেবা পৌঁছে দেওয়া, NID, BRN, অনলাইন পাসপোর্ট আবেদন, সার্বজনীন জন্মনিবন্ধন ব্যবস্থা, ই-পেমেন্ট গেটওয়ে ও মোবাইল ব্যাংকিং সেবার প্রসার এসব উদ্যোগ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তবে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে।
চ্যালেঞ্জসমূহ- ডিজিটাল বিভাজন (Digital Divide)-শহর ও গ্রামের মধ্যে ইন্টারনেট ও প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবধান এখনও অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে ই-গভর্ন্যান্সের সুফল সর্বস্তরে পৌঁছায় না। সক্ষমতা ও দক্ষতার ঘাটতি- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনেকেই প্রয়োজনীয় আইটি দক্ষতা না থাকায় অনেক সময় প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি হয়। সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি- ব্যক্তিগত তথ্য ও সরকারি ডেটাবেইস নিরাপদ না থাকলে সাইবার হামলা বা তথ্যচুরি হতে পারে, যা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়হীনতা- বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানে সমন্বয়ের অভাব ই-গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে।
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও করণীয় বাংলাদেশসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ই-গভর্ন্যান্সের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আস্থা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন, এবং প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ: আইটি অবকাঠামোর উন্নয়ন (বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে),প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা, সাইবার নিরাপত্তা আইন ও কার্যকর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বহুমাত্রিক অনলাইন অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি (যেমন, নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত অনলাইন ভোটিং), একীভূত তথ্যভান্ডার ও আন্তঃদপ্তর সমন্বয় নিশ্চিত করা।
ই-গভর্ন্যান্স গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। এটি জনগণের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংযোগকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করে তোলে। যদিও চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তবে সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে ই-গভর্ন্যান্স শুধু একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন নয়, বরং গণতান্ত্রিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশও এই সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।
লেখক-
প্রভাষক- প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজ
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।